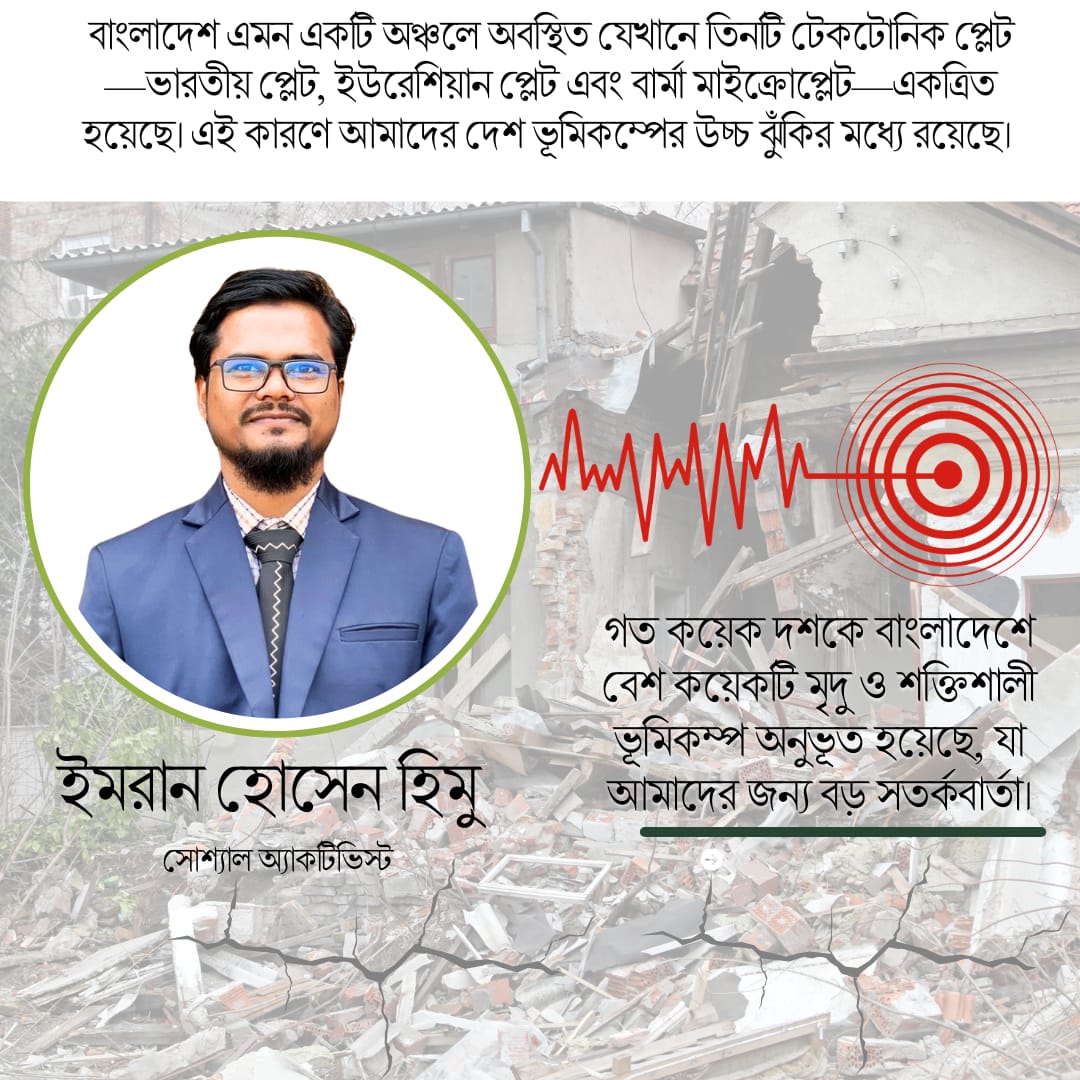দক্ষিণ এশিয়া ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। ভূতাত্ত্বিক গবেষণা বলছে, বাংলাদেশ এমন একটি অঞ্চলে অবস্থিত, যেখানে তিনটি টেকটোনিক প্লেট—ভারতীয় প্লেট, ইউরেশিয়ান প্লেট এবং বার্মা মাইক্রোপ্লেট—একত্রিত হয়েছে। এই কারণে আমাদের দেশ ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। গত কয়েক দশকে আমরা বেশ কয়েকটি মৃদু ও শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভব করেছি, যা আমাদের জন্য বড় সতর্কবার্তা।
ভূমিকম্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৭৬২ সালে চট্টগ্রামে ৮.৫ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল, যার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি দেবে যায় এবং বিশাল সুনামি সৃষ্টি হয়। ১৮৯৭ সালের গ্রেট আসাম ভূমিকম্পও আমাদের অঞ্চলে বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। এরপর ১৯৫০ সালের আসাম ভূমিকম্প, ২০০৩ সালের মেঘালয় ভূমিকম্প এবং ২০১১ সালের মিয়ানমারের ভূমিকম্প আমাদের স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে আমরা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছি।
বর্তমানে, ভূমিকম্পের দিক থেকে দেশের কোন কোন এলাকা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে, তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার উপকূলীয় অঞ্চল সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এখানে ভারতীয় ও বার্মা প্লেটের সংযোগস্থল রয়েছে। সিলেট অঞ্চলও উচ্চ ঝুঁকিতে, কারণ এটি ভারতের শিলং প্লাটো ও আসাম ফল্টের নিকটবর্তী। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই অঞ্চলে প্রতি ১০০ বছরে একটি বড় ভূমিকম্প ঘটে থাকে। ঢাকাও ঝুঁকির বাইরে নয়, কারণ এটি বেশ কয়েকটি সক্রিয় ফল্ট লাইনের উপর অবস্থিত। ঢাকা জনবহুল শহর হওয়ায় ৬-৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে।
কিন্তু কেন এই ভূমিকম্প হয়? ভূবিজ্ঞানীদের মতে, ভারতীয় প্লেট প্রতিবছর প্রায় ৪৬ মিলিমিটার গতিতে ইউরেশিয়ান প্লেটের নিচে প্রবেশ করছে। এই চলাচল বিভিন্ন ধরনের ভূমিকম্প সৃষ্টির কারণ হতে পারে। চট্টগ্রাম-ত্রিপুরা ফল্ট, ঢাকা ফল্ট এবং আসাম ফল্টের মতো সক্রিয় ফল্ট লাইনগুলোর কারণে ভবিষ্যতে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই অঞ্চলে ৭.৫ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প ঘটতে পারে, যা ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনবে।
এমন পরিস্থিতিতে আমাদের কী করণীয়? ভূমিকম্প প্রতিরোধের জন্য সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। ভূমিকম্প প্রতিরোধী নির্মাণ কোড (BNBC 2020) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জরুরি উদ্ধার ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাড়ানো হয়েছে এবং ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। তবে এসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন ঠিকমতো হচ্ছে কি না, সেটি নিশ্চিত করাটাও জরুরি।
আমাদের ব্যক্তিগতভাবেও সচেতন হতে হবে। আমরা কি জানি, ভূমিকম্পের সময় কী করা উচিত? জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক আছে তো? আমাদের বাসায় কি ভূমিকম্পের জন্য জরুরি মেডিকেল কিট, শুকনো খাবার ও পানি সংরক্ষণ করা আছে? আমরা কি জানি, ভূমিকম্পের সময় কোথায় আশ্রয় নেওয়া উচিত? বহুতল ভবনের বাসিন্দাদের জন্য ভূমিকম্পের সময় নিরাপদ বহির্গমন পথ জানা অত্যন্ত জরুরি।
ভূমিকম্পের পূর্বে, চলাকালীন এবং পরে করণীয়:
ভূমিকম্পের পূর্বে:
◑ জরুরি পরিকল্পনা তৈরি করুন – পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভূমিকম্পের সময় করণীয় বিষয়ে আলোচনা করুন।
◑ নিরাপদ আশ্রয়স্থল চিহ্নিত করুন – ঘরের শক্তিশালী আসবাবের নিচে বা দরজার ফ্রেমের নিচে আশ্রয় নেওয়ার জায়গা নির্ধারণ করুন।
◑ জরুরি কিট প্রস্তুত রাখুন – পানীয় জল, শুকনো খাবার, ওষুধ, টর্চলাইট, ব্যাটারি, মোবাইল চার্জার ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র একটি ব্যাগে রাখুন।
◑ নির্মাণ কাঠামো পরীক্ষা করুন – ভূমিকম্প সহনীয় কি না, তা নিশ্চিত করুন। পুরনো ভবনের রেট্রোফিটিং (পুনর্গঠন) করুন।
◑ গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ চেক করুন – ভূমিকম্পের সময় এগুলো বিপজ্জনক হতে পারে।
ভূমিকম্পের সময়:
◑ ডাকুন, ঢাকুন, আটকে ধরুন (Drop, Cover, Hold) – মেঝেতে বসুন, শক্ত আসবাবের নিচে ঢুকে পড়ুন এবং শক্তভাবে ধরুন।
◑ দেয়াল বা জানালা থেকে দূরে থাকুন – জানালা, আয়না, আলমারি বা যেকোনো ভেঙে পড়তে পারে এমন বস্তু থেকে দূরে থাকুন।
◑ সিঁড়ি বা লিফট ব্যবহার করবেন না – ভবন কাঁপতে থাকলে সিঁড়ি বা লিফট ব্যবহার বিপজ্জনক হতে পারে।
◑ বাইরে থাকলে খোলা জায়গায় যান – ভবনের ধ্বংসাবশেষ, বৈদ্যুতিক খুঁটি বা বড় গাছের নিচে দাঁড়াবেন না।
◑ গাড়িতে থাকলে রাস্তার পাশে থামুন – ওভারব্রিজ, ফ্লাইওভার ও বড় বিল্ডিং থেকে দূরে থাকুন।
ভূমিকম্পের পরে:
◑ নিজেকে এবং আশপাশের মানুষকে নিরাপদ করুন – আহতদের চিকিৎসা দিন এবং জরুরি পরিষেবার সহায়তা নিন।
◑ গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ পরীক্ষা করুন – লিক বা শর্ট সার্কিট থাকলে দ্রুত সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানান।
◑ আফটারশক সম্পর্কে সতর্ক থাকুন – ভূমিকম্পের পরে ছোট ছোট কম্পন হতে পারে, যা বিপজ্জনক হতে পারে।
◑ নিরাপদ স্থানে অবস্থান করুন – যদি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সেটিতে না ফিরে নিরাপদ স্থানে যান।
◑ গুজবে কান দেবেন না – ভূমিকম্প সম্পর্কিত তথ্যের জন্য সরকারি ও নির্ভরযোগ্য সংবাদ মাধ্যম অনুসরণ করুন।
নির্মাণ নিরাপত্তার দিক থেকেও আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন তৈরি করতে হবে, পুরনো ভবনগুলোর সংস্কার করতে হবে। দক্ষ প্রকৌশলীদের পরামর্শ নিয়ে ভবন নির্মাণ করতে হবে। পাশাপাশি, সরকারের ভূমিকম্প মোকাবিলায় নেওয়া পরিকল্পনাগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
সচেতনতা বাড়ানোর জন্য গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্কুল, কলেজ এবং অফিসে ভূমিকম্প মহড়া পরিচালনা করা উচিত, যাতে মানুষ জানে, কীভাবে নিজেদের নিরাপদ রাখতে হয়।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা ভূমিকম্প পূর্বাভাস আরও উন্নত করতে পারি। বাংলাদেশ সরকার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো এ নিয়ে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে, ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হবে।
ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তবে যথাযথ প্রস্তুতির মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব। এখন সময় আমাদের উদ্যোগ নেওয়ার, যাতে আগামীর ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়।
লেখক: সোশ্যাল অ্যাকটিভিস্ট

 ডেক্স রিপোর্ট
ডেক্স রিপোর্ট